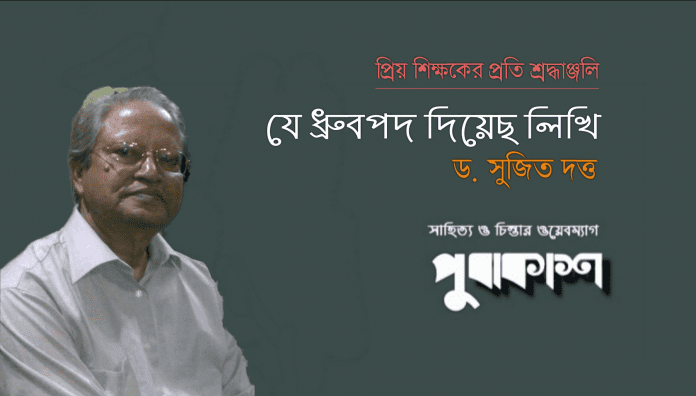প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
যে ধ্রুবপদ দিয়েছ লিখি
ড. সুজিত দত্ত ।। পুবাকাশ
এক.
“Thus I entered, and thus I go!” রবার্ট ব্রাউনিং এর Patriot কবিতার লাইনটি মনে পরে গেলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে যে ক’জন বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রারম্ভিক বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠিত করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তাঁদের অন্যতম। তিনি এসেছিলেন বীরদর্পে। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক অবস্থান থেকে–প্রথমে ইংরেজি বিভাগের সভাপতি, পরবর্তীতে কলা অনুষদের ডিন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হিসেবে – তাঁর নানান গঠনমূলক দিকনির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় একাডেমিক এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে তাঁর অসামান্য অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। নিভৃতচারি এই মানুষটি আজ কিছুটা অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়ে চলে গেলেন নীরবে, সবার অলক্ষ্যে। অসাধারণ মেধা ও মনন, অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ত্ব ও মার্জিত রুচির অধিকারি সৌম্য-দর্শন, সুমিষ্ঠভাষি, হাজারো ছাত্র-ছাত্রির প্রাণ-প্রিয় শিক্ষক শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী।
তাঁর মৃত্যুর পর কিছু প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিচারণ ছাড়া, পরিতাপের বিষয়, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শোকবার্তা, কিংবা একাডেমিক পরিমণ্ডলে তাঁকে নিয়ে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত আমার চোখে পরেনি। প্রবাদপ্রতিম একজন শিক্ষকের নীরব প্রস্থান ! এমনটি তো হওয়ার কথা ছিলোনা। প্রশ্ন জাগে মনে — বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে মহীরুহের ছায়াতলে বসে আমরা আজ জ্ঞানের সাধনা করছি, যার ফুলের সুবাস বাতাসে ছড়াচ্ছে বিশ্বময়, যার ফল আমরা আজ উপভোগ করছি দেশে ও দেশের বাইরে, সেই মহীরুহের বীজ যে মালি বপন করেছিলেন তাঁর কাছে কি আমাদের কোন ঋণ নেই? তবে কেন এমন হলো? এ অবস্থার জন্যে দায়ী কে? স্যার নিজে? নাকি আমাদের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা? নাকি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান দলীয় রাজনীতি — যা শিক্ষক সমাজে বিভাজন এবং সহকর্মিদের মধ্যে অনাখাঙ্খিত বৈরিতা ও পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি করে উচ্চশিক্ষার মানকে ক্রমশঃ নিম্নগামি করে তুলছে?
১৯৭০ সনের মাঝামাঝি সময়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার ক’মাস আগের কথা। আমি চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম বর্ষ ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যারকে তখনো আমি চোখে দেখিনি, তবে কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের কাছে তাঁর কথা শুনেছি বিস্তর। তখন চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজি বিভাগে স্বনামধন্য অধ্যাপকবৃন্দের উপস্থিতি। অনার্সে আমাদের লেখাপড়া, বলা যায়, বেশ ভালোই চলছিলো। তবে কলেজের অনেক সহপাঠি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের কাছে প্রায়ই শুনতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশে পড়াশোনা করার ও সংস্কৃতি চর্চার সুবিধা অনেক বেশি। তাই আমারও ইচ্ছে করতো কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই। কিন্তু শঙ্কা দুটো–বিশ্ববিদ্যালয় কি আমাকে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ দেবে? দ্বিতীয়তঃ, কলেজ থেকে আমি কি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পাবো? ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না – কি করবো! একদিন দেখা করলাম কলেজে ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান সদা-হাসিমুখ, সুশীল সজ্জন, অনুরাগী শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ মাহতাবউদ্দিন স্যারের সাথে। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। পিতার কাছে পুত্র যেমন অকপটে সুপ্ত বাসনা খুলে বলে, আমিও আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তাঁর উপদেশ চাইলাম।
সব শুনে তিনি আমাকে বললেন, “তুমি তো জানো টি. সি. দেয়ার ব্যাপারে কলেজে একটি অলিখিত নিষেধাজ্ঞা চালু আছে; এ ব্যাপারে আমি না হয় অধ্যক্ষ সাহেবের সাথে আলাপ করলাম, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বিশ্ববিদ্যালয় কি তোমাকে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ দেবে? প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান; শুনেছি তিনি একজন “পারফেক্ট জেন্টলম্যান”। দেখা করে তোমার ইচ্ছাটা তাঁকে জানাতে পারো। আমার বিশ্বাস তিনি তোমার কথা শুনবেন এবং তোমাকে কোন একটা উপায় বলে দেবেন।“
মাহতাব স্যারের কথামতো একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ১৯৭০ সনের আগস্ট মাস। সঠিক তারিখ স্মরণে নেই। মনে নানা সংশয়–আলী স্যার তো আমাকে চেনেন না; তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি পাবো তো? উপরন্তু তিনি তো ব্যস্তও থাকতে পারেন মিটিং-এ কিংবা কোন অফিসিয়াল কাজে । তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখি। ভেতরে যাবার অনুমতি চাইতে তিনি বললেন, “কাম ইন।” রুমে ঢুকতেই চোখে পড়লো চেয়ারে বসা সৌম্যদর্শন, সুন্দর কান্তি, রাশভারী চেহারার প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। চোখে তাঁর পুরু চশমা, প্যান্টের ভেতরে ইন করা সাদা শার্ট, গলায় কালো টাই — যেমন সুদর্শন তাঁর চেহারা, তেমনি পরিপাটি বেশভূষা। দেখতেই আস্থায় এবং ভক্তিতে মস্তক আনত হয়ে আসে। সভয়ে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম নিজের অভিপ্রায়। প্রশ্ন করলেন কেন আমি কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাই। আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর “বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশে পড়ালেখার ও সংস্কৃতি-চর্চার সুযোগ বেশি, তাই।”
এর পর তিনি আমার এস-এস-সি ও এইচ-এস-সি পরীক্ষার ফলাফল এবং কলেজে আমাদের প্রথম বর্ষের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সব শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত ইতিবাচক; তিনি আমাকে ভর্তির অনুমতি দিলেন। টি সি-র ব্যাপারে কলেজের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার কথা জানালে তিনি বললেন, “আইনত কলেজ তোমাকে আটকাতে পারেনা।” এবার আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন প্রয়োজনে প্রফেসর মাহতাবউদ্দিন সাহেবের সাথে তিনি নিজে কথা বলবেন। আমার মনে হলো এ যেন অনেকটা মেঘ না চাইতে বৃষ্টি আসার মতো অবস্থা।
আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সেরে কলেজ থেকে টি, সি, নিয়ে দু’সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। নিজের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে মাহতাব স্যার ও আলী স্যারের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরে উঠলো। আমার অভিজ্ঞান হলো উদার-হৃদয় ও উন্নত মানসিকতার অধিকারি আলী স্যার ও মাহতাব স্যার এর মতো মহৎ ব্যক্তিরা অন্যের উপকার করতে সমস্যা চিহ্নিত করার সাথে সমাধানের পথ ও বলে দেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাহতাব স্যার না বললে আমি আলী স্যারের সাথে দেখা করতাম না, আর আলী স্যার মাহতাব স্যারের সাথে কথা বলার আশ্বাস না দিলে ট্রান্সফার নিয়ে আমার কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না।
কিংবদন্তি অধ্যাপক আলী স্যারের সাথে সেটাই আমার প্রথম সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাতে তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণা–তিনি একজন মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, সহানুভূতিশীল, এবং খোলামনের মানুষ যিনি বাইরে যেমন চৌকস এবং সুদর্শন, ভেতরেও তেমনি উদার, মহৎ এবং অকপট হৃদয়ের অধিকারী। কথা আছে “ফার্স্ট ইম্প্রেশন লাস্টস লং”। এর পর তাঁকে যত বেশি দেখেছি এবং জেনেছি–একজন অসাধারণ শিক্ষক হিসেবে, একজন অভিভাবক হিসেবে, একজন বরিষ্ঠ সহকর্মি হিসেবে, সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে–ততই তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি, তাঁর প্রতি তত বেশি আকৃষ্ট হয়েছি।
দুই.
আলী স্যারকে আমি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি অনার্সে এবং মাস্টার্সে । একজন নিবেদিতপ্রাণ, ছাত্রহিতৈষী, অনুকরণীয় এবং আদর্শ শিক্ষকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। আমার শিক্ষক হওয়ার পেছনে যাঁদের অবদান ও অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি, বলতে দ্বিধা নেই, আলী স্যার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আমার কাছে “রোল মডেল”। একটি ছোট ঘটনার কথা এখানে না বলে পারছিনা।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরি জীবনের দ্বিতীয় বর্ষে BCS পরীক্ষার আবেদন পত্র জমা দেব। আবেদন করতে হবে যথাযথ কতৃপক্ষের মাধ্যমে। ফর্ম-এ সুপারিশ নিতে আলী স্যারের কাছে গেলাম। তিনি সই করলেন না। বললেন, “বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তবুদ্ধি চর্চার জায়গা। সরকারি চাকরিতে সে স্বাধীনতা কি তোমার থাকবে ! এখানে তুমিতো বেশ ভালোই করছো। আমি চাই তুমি শিক্ষকতায় থেকে যাও। আজ বাসায় গিয়ে চিন্তা করে আগামিকাল এসে আমাকে জানাও। তুমি চাইলে আমি সই করে দেবো, তবে আই ওয়ান্ট ইউ টু গিভ এ সেকেন্ড থট টু ইট।” বাসায় ফিরে স্যারের উপদেশ নিয়ে অনেক ভাবলাম। তখনকার দিনে সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের মর্যাদা ছিলো গগনচুম্বি। বুঝতে পারলাম একজন একান্ত শুভাকাঙ্খি হিসেবে আমাকে স্নেহ করেন বলেই স্যার বিষয়টি নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে বলেছেন। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম BCS পরীক্ষার আবেদন পত্র জমা দেবোনা; বাকি জীবন শিক্ষকতা পেশাতেই কাটিয়ে দেবো। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে স্যারকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই তিনি স্মিত হেসে আমাকে বললেন, “সুজিত, তোমার সিদ্ধান্তে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং আমি জানি তুমি খুব ভালো শিক্ষক হবে”। সেইদিন আমার জীবনের যে গন্তব্য নির্ধারিত হয়েছিলো, অদ্যাবদি সেই পথেই চলছি, পরমানন্দে। আমি স্যারের কথা রেখেছি; তবে কতো ভালো শিক্ষক হয়েছি তার বিচার করবে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা।
অনার্সে আলী স্যার আমাদের Milton এর Paradise Lost, Coleridge এর কবিতা এবং মাস্টার্সে Middle English Lyrics, Chaucer এর “Canterbury Tales” এবং History of the English Language পড়াতেন। কেমন শিক্ষক ছিলেন আলী স্যার?
ফুলগুলো যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ও গন্ধে বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলে, তেমনি শিক্ষাঙ্গনে প্রত্যেক শিক্ষকই স্বকীয় বৈশিষ্ঠ্যে অন্যদের থেকে আলাদা — এই কথাটি আলী স্যারের বেলায় আরো বেশি প্রযোজ্য। তাঁর অসামান্য মেধা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর সাহিত্যানুরাগ এবং বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি ক্লাসে আমাদের সম্মোহিত করে রাখতো। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিচ্ছবি, তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য বিচারের ভিত্তি হওয়া উচিত সমাজবাস্তবতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। মূলতঃ “culture and theme-based approach”-এ তিনি আমাদের পড়াতেন। ওজস্বী গলায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে কবিতার লাইন আবৃতি করে Mariner-এর albatross হত্যার কৃত পাপজনিত গভীর অন্তর্দাহ মনোস্তাত্বিক বিশ্লেষণে প্রবল আবেগ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন; সেইসাথে সমাজবাস্তবতা ও নীতিবোধের নিরিখে তার মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতেন। গ্রীষ্মের দাবানলে বন পুড়ে যাবার দৃশ্য তখনো আমরা দেখিনি, তবে albatross হত্যা করায় অনুতাপের তীব্র অন্তর্দহনে Mariner-এর হৃদয় পুড়ে খান-খান হয়ে যাওয়ার চিত্র দেখেছি আলী স্যারের ক্লাসে। তাঁর বেশ-ভূষার পরিপাট্যের মতো বাক্যগঠনের সময় শব্দচয়নেও তাঁর “পারফেকশনিস্ট” দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়তো । পুষ্প-পসারিরা যেমন বহুবর্ণের ফুল সুতায় গেঁথে মালা সাজায়, আলী স্যারও তেমনি বেছে বেছে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতেন। আমাদের মনে দাগ কেটে যেত। Coleridge এর “Kubla Khan” কবিতাকে তিনি বলতেন “a phantasmagoria of unconnected visions of a sublime somnambulist”; তাঁর ভাষা ব্যবহারের যাদুকরী শক্তি আমাদের নিয়ে যেত কল্পলোকে — কবির স্বপ্নপুরি Xanadu-তে যেখানে সুন্দর এবং ভয়ঙ্করের মেলবন্ধন ঘটতো।
“Unlettered audience এর উদ্যেশে রচিত Middle English lyrics-এর সাউন্ড-এফেক্ট বা গীতিময়তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি টিপিক্যাল মধ্যযুগীয় ইংরেজি উচ্চারণে সুললিত কণ্ঠে কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনতাম। মনে হতো যেন কোন বিশিষ্ট শিল্পির লাইভ পারফরম্যান্স দেখছি। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় মধ্যযুগের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ ও লোকায়ত জীবনযাত্রার চিত্র সিনেমার পর্দার মতো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তাঁর আপাত-গম্ভীর চেহারার অন্তরালে ঢাকা থাকতো সহজাত প্রফুল্লতা ও রসিকতাবোধ। Chaucher-এর Canterbury Tales-এর তীর্থযাত্রিদের চরিত্র বিশ্লেষণে ফুটে উঠতো তাঁর সেই অন্তর্নিহিত রসবোধের পরিচয়। তিনি যখন ব্যাখ্যা করতেন “bonhomie rather than piety is the hallmark of Chaucer’s pilgrims”, তখন তাঁর নিজের অভিব্যক্তিতেই আমরা সেই প্রফুল্লতার স্বত:স্ফূর্ত বর্হিপ্রকাশ দেখতে পেতাম।
তিন.
কেমন ছিলেন আমাদের প্রিয় আলী স্যার ক্লাসের বাইরে, একজন মানুষ হিসেবে ! সাগরে মুক্তা থাকে, পাথরে হীরে থাকে যা সহজে আমাদের চোখে পরেনা। প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর গুরুগম্ভীর চেহারার অন্তরালে লুকিয়ে থাকতো এক উচ্ছল, প্রাণবন্ত, আন্তরিক ও সংবেদনশীল মানুষ যাঁকে আবিষ্কার করতে সময় লাগতো, তাঁর খুব কাছে যেতে হতো।
ছাত্রাবস্থায় আমরা ক’জন ক্লাসমেট মিলে মাঝে-মধ্যে স্যারের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে যেতাম তাঁর সাথে দেখা করতে। প্ৰথম দিকে খুব ভয় হতো তাঁর সাথে কথা বলতে। ক্ৰমশঃ আলাপের মাধ্যমে আবিষ্কার করলাম তাঁর ভেতরের মনুষটিকে — আন্তরিক, প্রাণোচ্ছল, স্নেহবৎসল, একান্ত আপনজন ।
অনেক সময় ছোট কাজেও মানুষের মহানুভবতা প্রকাশ পায়। এমনি একটা ঘঠনার কথা মনে পড়ে গেলো। ১৯৭৪ সনে মাস্টার্স পড়ার সময় আমি এফ, আর, হলে থাকতাম। একবার বন্ধুর সাথে নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপে বেড়াতে গেলাম। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, তাই খোলের বন্ধুদের জানাতে সময় পাইনি। এখানে বলে রাখা দরকার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা তখনো মোবাইল ও ইন্টারনেট এর মাইলফলক ছুঁতে পারেনি।
পরদিন গ্রামের বাড়ি থেকে আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসে বাবা দেখতে পান আমি হলে নেই। কারো কাছে কোন খবর না পেয়ে বাবা চলে গেলেন ইংরেজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ আলী সাহেবের বাসায়। আলী সাহেবকে তখনো পর্যন্ত তিনি চেনেননা। সব শুনে আলী স্যার বাবাকে আশ্বস্ত করলেন আগের দিন আমি তাঁর ক্লাসে ছিলাম। আমি ভালো আছি। হতে পারে আমি কোন বন্ধুর সাথে বেড়াতে গেছি। বাস-স্টপ পর্যন্ত এসে আলী স্যার বাবাকে শিক্ষকদের শহরগামি শপিংবাসে তুলে দিলেন। এসিস্ট্যান্টকে ডেকে আমার বাবাকে তাঁর নিজের গেস্ট হিসেবে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে নিউ মার্কেট পৌঁছিয়ে দিতে বললেন।
হাতিয়া থেকে ফিরে পরদিন ক্লাসে গেলাম। স্যার বিভাগের অফিসে মেসেজ রেখেছিলেন আমি যেন অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করি। গেলাম স্যারের রুমে। স্যার বললেন, “আজই বাড়ি গিয়ে তোমার বাবার সাথে দেখা করো। তিনি খুব চিন্তায় আছেন।” স্যারের কথা মতো বাড়ি গিয়ে বাবার সাথে দেখা করলাম। সেদিন বাবার মুখে আলী স্যারের সৌজন্যতার কথা শুনে স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিলো।
শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ক্লাসের ফাঁকে সময় পেলে আমি স্যারের সাথে গল্প করতে যেতাম বিভাগে তাঁর ২০১ নম্বর রুমে — কখনো একা, আবার কখনো অন্য সহকর্মিদের সাথে। কোন কোন সময় বাংলা বিভাগে তাঁর ক্লাস সেরে ম্যাডাম (স্যারের স্ত্রী অধ্যাপক খালেদা হানুম) ও উপস্থিত থাকতেন। আলাপ হতো, মুক্ত আলাপ–বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় রাজনীতি নয়, অন্য সহকর্মির সমালোচনা নয়; আলাপ হতো শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে। তাঁর মননশীল, নিরপেক্ষ, এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক অভিমত আমাদের ঋদ্ধ করতো। অক্সফোর্ডে তাঁর পড়াশোনার দিনগুলোর কথা বলতেন, তাঁর অধ্যাপকদের কথা বলতেন, তাঁর নানান অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনাতেন। বিখ্যাত লেখকদের নিয়ে লেখা মজার মজার “লিটাৱ্যারি এনেকডোটস” বলার সময় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিক সত্তাটি আমাদের সামনে ধরা দিতো যেমন করে গুটানো নির্মোক থেকে আপন অবয়বে বেরিয়ে আসে শামুক।
আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ে অন্য এক দিনের কথা। ক্লাসে যাবো, এমন সময় আমার ফোন বেজে উঠলো। “হ্যালো” বলতেই ওপার থেকে ভেসে এলো স্যারের কণ্ঠ “সুজিত, তুমি কি আমার রুমে একটু আসবে !” স্যারকে বললাম,”ক্লাসে যেতে বের হচ্ছি; এখন আসবো, না ক্লাসের পরে আসবো।” স্যার বললেন, “ক্লাস সেরে এসো।” ক্লাসের পর সরাসরি স্যারের রুমে গেলাম। যেতে যেতে ভাবছিলাম কি বিশেষ প্রয়োজনে স্যার আমাকে তাঁর রুমে যেতে বললেন। ঢুকতেই দেখি বসে আছেন স্যার এবং ম্যাডাম খালেদা হানুম। ম্যাডাম বললেন, “সুখবর আছে – বাংলা একাডেমির ডি, জি, হিসেবে তোমার আর এক শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর রশিদ Bengali-English অভিধান তৈরির যে প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন তা সম্পন্ন হয়েছে। তুমিতো জানো তোমার স্যার সেই অভিধান প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদের একজন সদস্য। অভিধানটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি কিছু সৌজন্য কপি পেয়েছেন। তোমার স্যারের ইচ্ছা প্রথম কপিটি তোমাকেই দেবেন।” স্যার ব্যাগ থেকে একটি কপি বের করে আমাকে দিলেন। প্রচ্ছদ খুলতেই চোখে পরলো স্যারের নিজের হাতের লেখা: To: Dr. Sujit K. Dutta, Erstwhile pupil, now an esteemed colleague. — Mohammad Ali.” অভিধানটি হাতে নিয়ে স্যারের স্নেহের বর্হিপ্রকাশ দেখে সেদিন এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিলো।
কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের পঠন-পাঠন বিস্তর, জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত, দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও+ মানসিকতা উন্নত। তাঁরা জ্ঞানের বাতিঘর। অন্যদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে কখনো তাঁরা বড় করে দেখেন না, উল্টো তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের আলোকে আশেপাশের সবাইকে আলোকিত করে তোলেন। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী যে তাঁদেরই একজন ছিলেন তার স্বপক্ষে আমি দুটো উদাহরণ এখানে তুলে ধরবো।
কথাটি শুনেছি প্রাচ্যভাষা বিভাগের এক সহকর্মির কাছে যাঁর Selection Committee-র অন্যতম সদস্য ছিলেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। আলী স্যার তাঁকে কালিদাসের নাটক “অভিজ্ঞান শকুন্তলম” এর উপর একটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সহকর্মি বলেছিলেন কালিদাসের উপর এমন একটি প্রশ্ন হতে পারে সেটা তিনি সংস্কৃতের সাহিত্যের একজন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবেও আগে কখনো ভাবেননি। ফলে কি করে উত্তর দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী তাঁকে clue দিয়ে সাহায্য করায় তিনি সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছিলেন এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নর্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন সেদিন আলী স্যারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহানুভবতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা তাঁর ছিলোনা। অনুরূপ চিত্র চোখে পরতো যখন স্যারের সাথে একই পরীক্ষা কমিটির Viva Board-এ কাজ করতাম। পরীক্ষার্থীরা স্যারের কিংবা অন্য কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে স্যার প্রায়ই আকারে ইঙ্গিতে তাদের সঠিক clue ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন যাতে তারা কিছু বলতে পারে। স্যার উল্টো আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, “তোমরা কোনটা চাও – শিক্ষার্থিরা যা জানেনা তাই পরীক্ষা করতে নাকি কতটুকু জানে তাই পরীক্ষা করতে ?”
ব্যক্তিত্ত্ব, বিচক্ষণতা ও বাক-চাতুর্যে আলী স্যারের সমকক্ষ মানুষ খুব একটা দেখা যায়না আমাদের সমাজে । স্বভাবে কিছুটা নিভৃতচারি প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর কাছে নিজের প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য কখনো প্রদর্শিনীর বস্তু ছিলো না, তবে প্রয়োজনে তিনি নির্ধ্বিধায় সত্য কথা বলতে পারতেন। মনে পড়ে গেলো সেই দিনের স্মৃতি –বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোয়া একটায় শহরে ফেরার সময়। কলা ভবনের সামনে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন সবাই — কেউ কেউ উপরের ছাউনি দেয়া ছোট স্ট্যান্ডে; স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাকিরা সবাই নিচে রাস্তার ধারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজগুলোতে ডিগ্রি পাস কৌর্সের ১০০ নম্বরের “Compulsory English” নিয়ে কথা হচ্ছিলো। নান মুনির নানা মত, তবে অধিকাংশই ইংরেজি তুলে দেয়ার পক্ষে। মতের স্বপক্ষে তাঁদের যুক্তি ১০০ নম্বরের ইংরেজি পড়ে কতটুকুই বা শেখা যায় ! জবাবে প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বলেছিলেন, “আমরা সবাই জানি Something is better than nothing; তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ একটু ছায়া পাবার আশায় ছোট ছাউনির নিচে আপনারা গাদাগাদি করে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন কারণ আপনারা বিশ্বাস করেন Some shade is better than no shade। অনুরূপ ভাবে ১০০ নম্বরের ফাঙ্কশনাল ইংলিশ কর্মক্ষত্রে কাজ চালিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সুতরাং আমরা কি বলতে পারিনা Some English is better than no English as some shade is better than no shade?” আলী স্যারের বিচক্ষণতায় সেই বিতর্ক সেখানেই থেমে গিয়েছিলো।
ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার ছেড়ে স্যারেরা চানগাঁও আবাসিক এলাকার বাসায় চলে আসার পর আমাদের যোগাযোগ আরো সহজ হলো। প্রায়ই যেতাম ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ করতে। ধীরপদে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতেন দুজন – স্যার ও ম্যাডাম । বসতেন পাশের সোফায়। আলাপ হতো, আড্ডা হতো, গল্প হতো। স্যার এবং স্যারের স্ত্রী উভয়েই সাহিত্যের অধ্যাপক। উভয়েই একনিষ্ঠ রবীন্দ্রানুরাগী। বার কয়েক স্যারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতও শুনেছি। স্যারের ভরা গলার পরিবেশনা বিশিষ্ঠ সংগীত শিল্পি দেবব্রত বিশ্বাসের (জর্জ-দা) কথা মনে করিয়ে দিতো। ম্যাডাম, স্যারের স্ত্রী অধ্যাপক খালেদা হানুম এক অমায়িক মহিলা ছিলেন। ধীরে, একটু নিচু স্বরে কথা বলতেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকতো। চা-পর্বে ঘরে বানানো হালকা নাস্তা নিবিড় আন্তরিকতায় নিজ হাতে আমার প্লেটে তুলে দিতেন। ভোলা কি যায় সেসব স্মৃতি !
আমি কানাডা আসার পরেও স্যার এবং ম্যাডামের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। ফোনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হতো। জন্মদিনে স্যারকে শ্রদ্ধা জানাতাম। দেশে গেলে আমার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও বাসায় গিয়ে দেখা করতাম। আড্ডা দিতাম। অবসর জীবনেও স্যারের জানার কৌতূহল দেখে বিস্মিত হতাম। জানতে চাইতেন আমি ক্লাসে কোন বিষয় পড়াই। একটা কোর্সে Hamlet পড়াই বলাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “বলো, কানাডিয়ান ক্লাসরুমে তুমি কিভাবে পড়াও?” আমি বলেছিলাম, “এখানে outcome-based লার্নিং এর প্রাধান্য। তাই টিচিং-লার্নিং পদ্ধতিকে more practical এবং more interactive করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রিদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়। আর সেই লক্ষ্যে প্রতি তিন ঘন্টার ক্লাস পিরিয়ডকে “Lecture” এবং “Activity” সেকশন-এ ভাগ করা হয় । এক্টিভিটি সেক্শনে টপিক-স্পেসিফিক কোয়েশ্চন-আনসার, গ্রুপ-ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন এবং ক্রিটিকাল ডিসকাশন প্রভৃতি কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। তাই টেক্সট এর উপর পাঠকের প্রিতিক্রিয়া জানার ক্ষেত্রে Reader Response Approach বেশি কার্যকরী মনে হয়। সেমেস্টার শেষে “Course outcome” এবং “Student-engagement” এর সামগ্রিক বিচারে অনলাইন Questionnaire এর মাধ্যমে কোর্সের সার্থকতা এবং শিক্ষকের এক্সেলেন্স এর পরিমাপ করা হয়। শুনে স্যার বলেছিলেন “বেশ ভালো সিস্টেম। আমাদের ছাত্র-ছাত্রিদের টেক্সট বই পড়ার প্রবণতা দিন দিন যেহারে কমে যাচ্ছে, তাতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও classroom teaching পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে।”
চার.
আমাদের সমাজের লোকায়ত ধারণা মতে পাঁচটি ব-কার বিযুক্ত বৈশিষ্ঠ–বিদ্যা, বাগ্মিতা, বপু, বস্ত্র, ও বৈভব–এর যে কোন একটি থাকলে মানুষ সম্মানের অধিকারি হয়। শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর মধ্যে সব বৈশিষ্ঠের বিরল সমন্বয় ঘটেছিলো, তবে পরিমাণে বৈভবের মাত্রা, বলা যায়, স্বাভাবিকভাবে কিছুটা কম ছিলো। আর সেজন্যেইতো মানুষকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় বিদ্যা এবং বিত্তের সহাবস্থান হয়না–লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এক ঘরে থাকেনা। অর্থের বৈভব না থাকলেও বিদ্যার বৈভব তাঁর পুরোমাত্রায় ছিলো। অভিজ্ঞতা, মননশীলতা, সাহিত্যানুরাগ ও অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর সমকক্ষ মানুষ সমাজে আজকাল খুব বেশি একটা দেখা যায় না। তারপরেও কথা থাকে। কোন মানুষই সমালোচনার উর্ধে নন। লোকে বলে চাঁদের গায়েও কালো দাগ আছে। আলী স্যারও এর ব্যত্যয় নন; তাঁর জীবনেও কিছু ব্যর্থতা ছিলো না একথা বলা যাবেনা। সেই সাথে এই কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে মানুষ অনেকসময় পরিস্থিতির শিকার হয়। হয়তো তিনিও হয়েছিলেন। আর তাই একজন মানুষকে তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই সমীচীন।
আমরা জানি একজন বড়ো লেখকেরও কিছু “মাইনর ওয়ার্কস” থাকে। কিন্তু সেই “মাইনর ওয়ার্কসের” মূল্যায়নের আলোকে ঐ লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের পরিপূর্ণ চিত্র কখনো পাওয়া যায় না।
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং অধ্যাপক খালেদা হানুম যেন মানিকজোড় – তাঁরা ছিলেন অভিন্ন হৃদয়। ক্লাসরুমের বাইরে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কখনো তাঁদের একা দেখেছি বলে মনে পড়েনা। তাঁদের মধ্যে ছিল চিন্তার সংযোগ, ভাবের সংযোগ এবং হৃদয়ের সংযোগ। স্যার চলে যাবার পর ম্যাডাম নিশ্চয়ই খুব অসহায় বোধ করছিলেন। ভাবছিলাম এই শূন্যতা বুকে নিয়ে কিভাবে তিনি দিন কাটাবেন। একইভাবে ওপারে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে স্যারও ডাক দিলেন ম্যাডামকে। ম্যাডাম এপার থেকে সে ডাক শুনে স্যারকে জানিয়ে দিলেন–“বিশ্ব সাথে যোগে যেথা বিহার / সেখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।” জীবনের সব মায়া ত্যাগ করে দশদিনের মাথায় পরপারে স্যারের সাথে অনন্ত যাত্রায় যুক্ত হলেন ম্যাডাম।
আজ এক অব্যক্ত বেদনায় চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, বুক ভারি হয়ে আসছে যখন ভাবি স্যার কোথায় ! ম্যাডাম কোথায় ! কোন সুদূরে এখন তাঁদের অবস্থান ! আমরা, তাঁদের গুণমুগ্ধরা, “স্মৃতিভারে” পরে আছি; “ভারমুক্ত” তাঁরা “এখানে নেই”। তাঁদের শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। তাঁদের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।তাই বলি–অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং অধ্যাপক খালেদা হানুম, তোমরা “যে ধ্রুবপদ দিয়েছ লিখি”, যে আলো দিয়েছ ছড়ায়ে তার ফলে চোখের সামনে না থাকলেও আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো তোমরা জেগে থাকবে অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে তোমাদের হাজারো ছাত্র-ছাত্রির মানসপটে । সম্ভবতঃ সেটাই ছিল তোমাদের মনের সুপ্ত বাসনা যা এ, পি, জে, আব্দুল কালামের সেই উক্তিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় “If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for me.”
সুজিত দত্ত : প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ।চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কানাডা অভিবাসী।