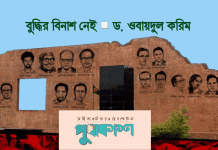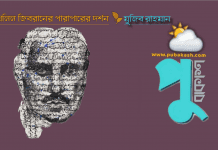রেফায়েত কবির শাওন
আমাদের আবাস ছিল রয়েল হলওয়ে ইউনিভার্সিটিতে। লন্ডনের শহরতলিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে অনেকেই লন্ডনের সবচেয়ে সুন্দর ক্যাম্পাস মনে করেন। সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে উনিশ কিলোমিটার দূরের এই বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৬ সালে তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির পঞ্চাশতম বার্ষিকিতে। সে সময় যে ভবনটি তৈরি করা হয় তাকে ঘিরেই পরবর্তিতে বেড়ে উঠে ১৪০ একর জায়গার উপর বিশাল ক্যাম্পাস। ফ্র্যাঞ্চ স্যাঁতোর আদলে তৈরি লাল ইটের বিশাল ভবনটিকে এখন বলা হয় “ফাউন্ডার্স বিল্ডিং” সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতাদের তৈরি বলেই এ ধরণের নামকরণ। উত্তর দক্ষিণে দুটি টাওয়ার সহ এই বিশাল স্থাপনার মধ্যে রয়েছে অফিসরুম, লেকচার হল, ডাইনিং হল, ছাত্র – ছাত্রীদের থাকার জায়গা এমনকি ভিক্টোরিয়ান আর্কিটেকচারে গড়া বড়সড় চ্যাপেল। আমাদের সৌভাগ্য আয়োজকরা আমাদের থাকার ব্যাবস্থা এই ভবনেই করেছেন। আমাদের শতবর্ষের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করেছেন।
আয়তকার ভবনের মাঝখানে খোলা ঘাসের লন তাতে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি। তার নিচে লেখা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছু তথ্য। ভবনটি এতই বড় যে এর যে কোন প্রান্ত থেকে হাঁটা শুরু করে আবার সে জায়গায় ফিরে আসতে মিনিট পনের সময় লেগে যায়। আমাদের রুম বরাদ্দ ছিল তৃতীয় তলার পশ্চিম অংশে। হিথরো থেকে আশার পথে বাসেই আমাদের রুমের ডিজিটাল চাবি হাতে তুলে দিয়ে নিয়ম কানুন বুঝিয়ে দিয়েছিল গাইড, সারা। এই ডিজিটালি কোডেড কার্ডখানা আমাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে সারাক্ষণ। এটি গলায় থাকলে নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাদের কোন প্রশ্ন করবে না। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারব ক্যাম্পাসের সর্বত্র, এমনকি ডাইনিং হলে খেতে গেলেও গলায় ঝুলানো থাকতে হবে কার্ডখানা। তাছাড়া লন্ডনের গলি ঘুপছিতে যদি আপনি কখনো হারিয়েও যান, পুলিশকে কার্ডখানা দেখালে ফিরে আসতে পারবেন ক্যাম্পাসে। তবে সবচেয়ে ঝক্কির ব্যাপার ছিল আপনি যদি রুমের ভেতর কার্ডখানা রেখে ওয়াশরুমেও যান তবে আপনি আর রুমেই ঢুকতে পারবেন না। বিকল্প কার্ড পাওয়া বেশ জটিল।
রুমে ঢোকার কিছু পরেই ডিনারের ডাক পরল। এখানে এখন সময় সন্ধা ছয়টা। আকাশে এখনো গনগনে রোদ। রাত নামতে দশটা বেজে যাবে। যা হোক ডিনারের জন্য যাত্রা করলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া যে বিল্ডিংয়ে হবে তার নাম “দি হাব” । ফাউন্ডার্স বিল্ডিং থেকে সেখানে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে মিনিট দশেক লেগে যায়। খেয়ে ফেরার পথে উঠতে হয় পাহাড়ের গা বেয়ে। ব্যাপারটা এমন যে খেয়ে ফিরে আসতে আসতে আবার ক্ষিদা লেগে যায়। তাছাড়া ইংলিশ ডিনারের বিস্বাদ খাওয়া আমাদের রোচে না। তাই সন্ধার এই ইংলিশ ডিনারকে আমরা বিকালের নাস্তা হিসেবে ধরে নিলাম। কিছু ফল, কেক আর চা’তো খাওয়া যায়। রাত দশটার দিকে আসত আমাদের জিভে জল আনা বাঙালী ডিনার। সিলেটের লোক বশির ভাই তার গাড়ীতে করে নিয়ে আসতেন কখনো চিকেন বিরিয়ানী, কখনো মাটন, কখনো বা কাবাব আর নান।
ডিনারের পর ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আসলে এর আকার এত বড় যে এক সন্ধায় এর কিয়দংশই দেখা সম্ভব। উঁচু নিচু টিলার গায়ে, নিপুণ দক্ষতায় ভবনগুলো ডিজাইন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশটি ডিপার্টমেন্টের প্রতিটিই আলাদা আলাদা ভবনে। তাছাড়া আছে বেশকিছু আবাসিক ভবন, স্পের্টস সেন্টার, লাইব্রেরি, ডিপার্টমেন্ট স্টোর, ব্যান্ক, বেশ কয়েকটি ক্যাফে, নাটকের জন্য থিয়েটার হল, অডিটোরিয়াম প্রভৃতি। প্রতিটি ভবনের নামকরণ করা হয়েছে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষদের নামে। আমাদের দেশে হলে নেতা নেত্রীদের নামেই করতে হত। ভবনগুলির অবস্থান বেশ দুরে দূরে এবং মাঝখানে গাছপালায় ঘেরা হাঁটা পথ। অবশ্য ঘুর পথে প্রতিটি ভবনেই গাড়ী নিয়ে যাওয়া যায়। ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে মনে হয় কোন জঙ্গলে না এসে পড়লাম। রয়েল হলওয়ের ক্যাম্পাসে রয়েছে দূ’শোরও বেশী প্রজাতির গাছ। পরিবেশ যত্নে পুরস্কৃতও হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।
হাঁটতে হাঁটতে কাঁচঘেরা আধুনিক একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে পৌছুলাম। জানতে পারলাম এটা লাইব্রেরী ভবন। চারতলা এই লাইব্রেরী ভবন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড়। পাঁচ লক্ষেরও বেশি বইয়ে ঠাশা এই বিশাল লাইব্রেরী ভবেনের পড়ার জায়গা গুলো ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়ানো। আপনি যদি একা একা পড়তে চান আপনি যাবেন এক দিকে। গ্রুপ স্টাডির জন্য অন্যদিকে। আরেকপাশে একখানা বই হাতে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে খোলা প্রান্তরের দিকে মূখ করে বসতে পারেন। পড়তে পড়তে টায়ার্ড লাগলে, সবুজের দিকে তাকিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলেন না হয়।
লাইব্রেরীর সামনে খোলা চত্বরে বসে পরলাম। চত্তরটি পাকা আর চারধারে কংক্রিটের ব্যাঞ্চ। একপাশ গ্যালারীর মত। বোঝাই যায় ওপেন এয়ার প্রোগ্রামের জন্য ডিজাইন করা। চত্বরে বসে আকাশের দিকে তাকাতেই ভিন্ন এক দৃশ্য। আকাশ ভর্তি প্লেন। যেন অস্ংখ্য ঘুড়ি উড়ছে। আসলে রয়েল হলওয়ে ক্যাম্পাস হিথরো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি আর হিথরো পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর। এখানে প্রতি দেড় মিনিটে একটি বিমান ওঠে বা নামে। এগুলোর ছোটাছোটি দেখে রীতিমত ভয় লেগে উঠল। কখননা একটা আরেকটাকে ধাক্কা দেয়। কিন্তু না, অসাধারণ দক্ষতায় উড়ছে নানা দেশের নানা সংস্থার বিমানগুলো। ওরাতো আর আমাদের দেশের বাস ট্রাকের ড্রাইভার না যে ধাক্কা লাগিয়ে, মানুষ মেরে বাহবা পাবে।
অন্ধকার নামতে ফিরে এলাম ফাউন্ডার্স বিল্ডিঙে নিজের রুমে। হাতমুখ ধুয়ে শুতে যাব। এ ফ্লোরে আটচল্লিশটি রুমে আটচল্লিশজনের থাকার ব্যাবস্থা কিন্তু প্রক্ষালন কক্ষ মাত্র ছয়টি। দেড়শ বছরের পুরোন ভবনের অভ্যন্তরটা আধুনিকায়ন হয়েছে। রুমের দরজায় লেগেছে ডিজিটাল তালাচাবি, করিডোরে প্রবেশ পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড। ক্যামেরা থেকে, ফায়ার এলার্ম সবই আধুনিক, শুধু পবিত্র হওয়ার জায়গাটুকু সেকেলে। ইংরেজ জাতীর সভ্যতার সঙ্কট বুঝতে তাদের হেঁসেল আর প্রক্ষালন কক্ষ যথেষ্ঠ। এ দূঃখেই হয়ত রেগে চিতকার করেছিলেন বার্নার্ড শ, বিটলস গান গেয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছে অর্থহীন আভিজাত্যকে।
ঐতিহাসিক ভবনের ঐতিহাসিক কক্ষে রাতে ঘুম আসছিল না। প্রচন্ড গরম। ভাগ্য ভাল বিপরীত দিকের রুমগুলোও আমাদের দলের। মুখোমুখি রুমগুলোর দরজা খোলা রেখে, অপর পাশের জানালাগুলো থুলে এয়ার সার্কুলেশনের পথ করে কোনভাবে রুমগুলোকে বাসযোগ্য করে তুলি। আসলে কয়েকবছর আগেও বৃটিশ সামার ছিল আমাদের শীতকালের মত। তাই এখানকার বাড়ীগুলোকে গরম আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হয় নি। কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর চাপে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এই দেশ।
কথন ঘুমিয়ে পরি খেয়াল করিনি। হঠাত প্রচন্ড শব্দে ঘুম ভাঙে। করিডোরে বেরিয়ে আসতে দেখি এক ইংরেজ তরুনী চিতকার করে বলছে বেরিয়ে যেতে, ফায়ার এলার্ম বাজছে। অবশ্য অল্প কিছু্ক্ষণের মধ্যেই সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয়। আসলে ওয়েল্ডিং মেশিনের স্পার্ক এর কারণে বেজে ওঠে এলার্ম। রুমে ফিরে আসতে অনুভব করলাম প্রকৃতি কিছুটা ঠান্ডা হয়ে উঠেছে। বিছানায় পরতেই ঘুম।
অক্সফোর্ডে
আমেরিকানরা নাকি প্রতি দশটি বাক্যের নয়টি বলে গাড়ি নিয়ে আর বৃটিশরা আবহাওয়া নিয়ে। আমার আমেরিকান বান্ধবি জেসা কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদের গাড়ি নিয়ে এরকম অস্থিরতার কারণ। জবাবে সে বলেছিল, স্ধাধীনতা যুদ্ধ আর গৃহযু্দ্ধের কষ্ট তাদেরকে স্ধাধীনচেতা করে তুলেছে। আর গাড়ী তাদের কাছে স্ধাধীনতার প্রতিক। আর বৃটিশদের আবহাওয়া নিয়ে ব্যাকুলতার কারনটি শিখতে আমাকে যেতে হয়েছিল খোদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুনেছিলাম বৃটিশ সামার আমাদের দেশের শীতের মত। তবে আসার আগে প্রবাসী বন্ধু বান্ধবরা জানিয়েছিল এ বছর বৃটেনের গ্রীস্ম মধ্যপ্রাচ্যকে হার মানায়। হালকা টি শার্ট পরে হাঁটছিলাম অক্সফোর্ডের রাস্তায়। পুরোন সব দালানে পুরোন সব কলেজে পড়ানো হয় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান। তবে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ যেখানে যান না কেন, পাশে একটা বিশাল মার্কেট থাকবেই। বৃটিশদের ব্যবসায় বুদ্ধির কাছে সব কিছুই হার মানে। এদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও টুরিস্ট এট্রাকশন। বেড়াতে গেলে পর্য়টক যাতে গাঁটের পয়সাও কিছু খরচ করে তার ব্যবস্থা সর্বত্র।
প্রচন্ড গরমে অক্সফোর্ডের প্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, সকালের স্বাস্থ্য সম্মত ইংলিশ ব্রেকফাস্টের কিছুই মুখে রোচে নি। ক্ষুধা তৃষ্ঞা নিবারনে ঢুকে পড়লাম মেগডোনাল্ডসে, বার্গারের সাথে কোকাকোলা। এদেশের কোকাকোলা বড়ই স্বাদের। অসংখ্য বরফের টুকরো মেশালেও এর তৃপ্তির ঘাটতি হয় না। ঠান্ডা কোকাকোলায় চুমুক দিতে দিতে দেখি বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। বেরোতেই হাঁড় কাপানো শীতের কামড়। আধঘন্টা আগেও গরমে সেদ্ধ হচ্ছিল পুরো রাজ্য। আমাদের আজকের গাইড পোর্টসমাউথের মেয়ে সল্পবসনা এলি তার ব্যাকপ্যাক থেকে স্পোর্ট্স জ্যাকেট বের করতে করতে মুচকি হেঁসে জানাল এটাই বৃটিশ আবহাওয়া। বুঝলাম এদেশের মানুষ কেন সুযোগ পেলেই আবহাওয়ার পিন্ডি চটকায়। তড়িঘড়ি স্টারবাকে ঢুকে পরলাম। একটু আগে কোকাকোলা খেয়ে ঠান্ডা হয়েছি, এখন আবার একটু উস্ঞতার জন্য চুমুক দিতে হচ্ছে স্টারবাকের কফিতে।
গাছপালা ঘেরা একটা সরু রাস্তার একপ্রান্তে বাস থেকে নেমে হাটছিলাম আধুনিক বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। এখানকার ছাত্র – ছাত্রীরা সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়। মহাত্মা গান্ধী থেকে ইন্দিরা গান্ধী, আর সাম্প্রতীক ড. মনমোহন সিং – ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছেন আরো অনেক অক্সফোর্ড স্কলাররা। লিয়াকত আলি খান, বেনজরি ভুট্রো, আর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেট তারকা বর্তমান প্রধানমন্ত্রি ইমরান খানও অক্সফোর্ডের ছাত্র। শ্রিলংকা, থাইল্যান্ড, মালেশিয়ার নেতৃত্বেও ছিলেন অনেক অক্সফোর্ড স্কলার, সিঙ্গাপুরের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমনকি ভুটানের রাজপরিবারের অনেক সদস্যও এখানকার ছাত্র। প্রতিবেশিদের মধ্যে আমাদের আর মায়নমারেরই কখনো অক্সফোর্ড স্কলারের প্রয়োজন হয়নি যদি হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দির অল্প কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়াকে হিসেবে না নেই। অবশ্য অক্সফোর্ড স্কলারের কথা আসছে কেন, কোন স্কলারই যাতে রাজনীতির ধারে কাছে ঘেঁসতে না পারে সে ব্যবস্থা মোটামুটি পোক্ত। তারচেয়েও এগিয়ে এমন ব্যবস্থা হচ্ছে যেন বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কলার তৈরিই করতে না পারে। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত, এখানকার সত্যেন বোসদের গবেষণায় ইশ্বরকণার মত আবিস্কার সম্ভব হয়েছে। এখানকার গোবিন্দ চন্দ্র দেবরা ঔপনিবেশিক শাষকদের তাদের মেধার কাছে নত হতে বাধ্য করেছিল। আজ সেই অধ্যাপকরা কোথায়? দূর্নিতিবাজ রাজনীতিকদের প্রসংশা করতে করতে গবেষণার সময় তাদের নেই।
অক্সফোর্ড ক্যাম্পাসে ঢুকে প্রথমেই গেলাম বলডিয়ান কলেজে। দরজায় বেজায় ভীড় । বিখ্যাত হ্যারি পটার ছবির শুটিং হয়েছিল এই বিল্ডিয়ে তাই টুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণও এটি। এ কলেজের ভেতর ঢুকতে হলে এ যাত্রায় আর অক্সফোর্ডের অন্য কিছু দেখা হবে না। তাই আশপাশটা একটু ঘুরে, বিশাল ঘাসের লনে ঘেরা কুইনস কলেজ পেরিয়ে একটি বনমত জায়গায় এসে পৌছুলাম। অসংখ্য চিত্রল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে জায়গাটা জুড়ে। আরেকটু আগাতে কেয়ারী করা বিশাল ফুলের বাগান। আধুনিক বৃটেনের যতটুকু দেখেছি গাছগাছালি, ফুল আর ঘাসের কোন অভাব নেই। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পরলাম মেগডেলান কলেজে। আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হল এখানকার শিক্ষা আর গবেষণা পদ্ধতি।
অক্সফোর্ডের পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, ক্যাম্পাসের আকার আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোন অংশে কম নয়, হয়ত অক্সফোর্ড কেমব্রিজের মত এত বড় ঐতিহ্যের ধারক এখনও হতে পারে নি। একটু পরিচর্য়া, একটু যত্ন হয়ত এটিকেও করে তুলতে পারত টুরিস্ট এট্রাকশন। তবে শুধু অক্সফোর্ড কেমব্রিজ নয়, বিলেতের যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গিয়েছি সবখানেই দেখেছি, লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা। একদিন মাঝরাতে হাটতে হাটতে রয়েল হলওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে পৌঁছে দেখি পুরো ভবনটি আলোকিত। লাইব্রেরির বিভিন্ন প্রান্তে এখনও পড়ছে অনেকে। যারা পড়ছে তাদের মধ্যে সাদা ইউরোপিয়ানের চেয়ে, চাইনিজ কোরিয়ানদেরই দেখলাম সংখ্যায় বেশি। বুঝতে বাকি রইল না আগামী পৃথিবীর নেতৃত্ব কারা দেবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিই নয়, একদিন শহরতলির রাস্তায় হাটতে হাটতে পৌঁছি এগহাম লাইব্রেরি। ছিমছাম দোতলা বিল্ডিং, ইচ্ছেমত বই পড়া যায়, বাড়িতে নিয়ে পড়া যায় যত ইচ্ছা। এসব দেশে বইয়ের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সরকার। ভাবতে দূ:খ হল, আমার শহরে দূটো পাবলিক লাইব্রেরির একটা মৃত, আরেকটাও টিকে আছে অযত্ন, অবহেলায়।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশটি কলেজের প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিক্ষা গবেষনায় এখনো বিশ্বে নেতৃত্ব দেয় এই প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্যের অবক্ষয় নিয়ে আমাদের অনেক সমালোচনা। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি পাশ্চাত্যের যে মমত্ববোধ তার কি কিয়দংশও আমাদের আছে। নোয়াম চমস্কিরা যতই সমালোচনা করুক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যাক্তি কিন্তু তাকে জেলে পুরছে না। পত্রিকায় সত্য মিথ্যা যাই লিখুক, আইন করে নিজকে রক্ষা করতে হয় না এদের। প্রতিশোধস্পৃহায় টুকরো টুকরো করতে হয় না সাংবাদিকের মরদেহ। এই প্রাচ্য যতই অতীত গৌরবের অহংকার করুক, পাশ্চাত্যের মত জ্ঞান আর জ্ঞানীদের সম্মান করতে না শেখা পর্য়ন্ত পরাজিতই থেকে যাবে।
ক্যামব্রিজ
মহাযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক লন্ডনের রাস্তা কিন্তু জার্মানির দখলে। বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ, ম্যান, ভক্সওয়াগন, অডি – ছোট বড় হেন জার্মান গাড়ী নেই যেটি ছুটছে না বৃটেনের রাস্তায়। বিচিত এই বৃটিশ মোটর সোসাইটিতে আমেরিকা, ইউরোপের অন্যান্য দেশ, জাপান আর হালে কোরিয়া ও ভাগ বসিয়েছে, তবে সংখ্যায় আর মানে সবাই জার্মানদের পেছনে। ছোট বেলায় তিন গোয়েন্দা বইতে পড়া লস এন্জেলেসের কাছে রকি বিচের পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে কাজ করত দুই বিশাল দেহি ব্যাভারিয়ান। কিশোর মুসা রবিনকে কোন সন্ত্রাসী আক্রমন করতে আসলে আগলে রাখত তারা। তখন ভেবেছিলাম ব্যাভারিয়া আমেরিকার কোন জায়গা হবে হয়ত। অনেক পরে জেনেছি ব্যাভারিয়া জার্মানিতে আর এটি জনপ্রিয় কার ব্রান্ড বিএমডব্লিউর জন্মস্থান। ব্যাভারিয়া থেকেই এর নাম বিএমডব্লিউ (ব্যাভারিয়ান মোটর ওয়ার্কস)। ব্রিটনদের প্রিয় ছোট গাড়ী মিনি। অস্টিন মিনি থেকে মিনি হয়ে যাওয়া এই বিলেতি গাড়ির কোম্পানির মালিকও এখন জার্মান বিএমডব্লিউ।
সুন্দরবনে যেমন হরিণ, বানর, কুমিরের ভীড়ে বনের রাজা রয়েল বেঙল টাইগারের দেখা পাওয়া দূস্কর, তেমনি রাজার দেশ বৃটেনের রাস্তায় রাজকীয় রোলস রয়েসের দেখা পাওয়াও যায় কালে ভদ্রে। তবে বিশাল বিশাল রেন্জ রোভারদের রাস্তা কাঁপানো গতি মাঝে মাঝে জানান দেয় গাড়ীর দুনিয়ায় বৃটেন এখনও চুরান্ত পরাজিত হয়নি। Corbell of London কোম্পানির জার্মান MAN ব্র্যান্ডের বাসে চেপে কেমব্রিজ যাওয়ার পথে রাস্তার দূপাশে তাকিয়ে সত্যি মনে হল, হিটলার পরাজিত হলেও বিলেতের রাস্তার গতি নিয়ন্ত্রন করছে জার্মান গাড়িরা। এম ১১ হাইওয়ে ধরে ১০০ কিলোমিটারের রাস্তা পার হতে দুই ঘন্টাও লাগে নি। আমাদের আবাস রয়েল হলওয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের হতেই Ferrari গাড়ীর শো রুম। ভেতরে বাইরে পরে আছে অসংখ্য স্পোর্টস কার। প্রতিদিন যেতে আসতে এই দৃশ্য আমাদের দেখতে হত আর অধরা সপ্নের কথা ভেবে বুক চাপড়াতাম।
বাসে উঠতেই বৃদ্ধ ড্রাইভার ভারী গলায় জানাল সবাইকে সিট বেল্ট পরে নিতে। বলে কি, ব্যাটা নিশ্চয় আগে পাইলট ছিল। তবে রাশভারী বৃদ্ধের সাথে তর্ক করার সাহস হল না। ভদ্রলোকের মত সিট বেল্ট বেঁধে নিলাম। ড্রাইভার আবার জানাল, চলন্ত বাসে ভেতরে হাঁটা যাবে না। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। চলন্ত বাসের বাম্পারে ঝুলে পরাও আমাদের জন্য কোন ব্যাপার নয়। তারপরও সে অনড়, জানাল, গাড়ীতে দাঁড়ানো যাত্রি থাকলে তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। তর্ক না করে চুপচাপ বসে পরলাম। মানুষ খুন করা আমাদের দেশের বাস ড্রাইভারদের একটা খেলা, আর বোকা ইংরেজ ড্রাইভার আছে তার লাইসেন্স বাতিল হওয়ার টেনশনে।
দুঘন্টার যাত্রা পথে দু’পাশের দৃশ্য মোটামুটি একই, কিছু পর পর উঁচু নিচু টিলা। আর মাঝে মাঝে সোনালী শষ্য ক্ষেত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে গাড়ি বৈচিত্রই বেশি দৃশ্যমান। তবে বৃটিশ গাড়ি বহরের একটি ব্যাপার খুব অদ্ভূত। পৃথিবী যখন চালকবিহীন গাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন লন্ডনের রাস্তায় চলা অধিকাংশ গাড়ীই চলে ম্যানুয়েল গিয়ারে। এক অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদের এই আধুনিকতা বিমুখতার কারণ। হেসে জবাব দেন, তাঁদের গাড়ীর গিয়ারখানা ছাড়া আর সবকিছুই আধুনিক। ম্যানুয়েল গিয়ারে গাড়ী চালালে গতির উপর যেমন নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে তেমনি জ্বালানী খরচ আর পরিবেশের ক্ষতিও কম। কিছুটা রসিয়েই বললেন, আমেরিকানদের নিজেদের ইন্টেলিজেন্স বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই বলে তাদের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর উপর এত নির্ভর করতে হয়, তারা ম্যানুয়েল গাড়ি চালাতে পারে না। দেশে আমার লক্কর ঝক্কর মিতসুবিসি গাড়িখানা ম্যানুয়েল গিয়ারে চলে বলে অনেকে আমাকে ব্যাকডেটেড ভাবে, তাদের জন্য একখানা মোক্ষম জবাব পেলাম অধ্যাপকের কথায়। দশ বছর লন্ডনে প্রবাস কাটানো ছোট ভাই তান্না জানিয়েছিল বৃটেনে কেউ ম্যানুয়েল গিয়ারে গাড়ি চালাতে না পারলে তার লাইসেন্সে লিখে দেয়া হয়, সে শুধু অটো গিয়ারের চালক। এটা তাদের জন্য চরম অসম্মানের।
শুধু গাড়ীর গিয়ারের ক্ষেত্রে নয়, বৃটিশরা এখনো কয়েন বক্স টেলিফোন ব্যবহার করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল টেলিফোন বক্সগুলো দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম, এগুলো ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাখা। পরে জানলাম এর সবগুলোই ব্যবহার উপযোগী। ওরা এমনকি চিঠিও পোস্ট বক্সে ফেলে। পত্রিকায় পড়েছি জাপানের লোকজন এখনও ক্যাসেটে গান শোনে। কারণ তাদের পুরনো টেপ রেকর্ডারগুলো এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। আধুনিকতার নামে ভাল জিনিষ ফেলে দেওয়ার অদ্ভুত রোগ শুধু আমাদেরই আছে।
কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড ক্যাম্পাসে প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি কক্ষ এত বেশি ঐতিহ্য আর এত কাহিনীতে ঠাসা যে কোনটা ফেলে কোনটা বলব সিদ্ধান্ত নেয়া দূস্কর। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছুলাম কুইন্স কলেজের সামনে। এই কলেজের দুই অংশের মাঝে ছোট কেম নদী। নদীর উপর বিখ্যাত মেথমেটিকাল ব্রিজ। অনেকের ধারণা্ এই ব্রিজের মুল স্থপতি বিজ্ঞানী নিউটন, আসলে এর নির্মাণ নিউটনের মৃত্যুর পরে। উইলিয়াম এথরিজ এর ডিজাইনে, জেমস এসেক্স নির্মাণ করা এই ব্রিজের বেশিষ্ট্য হল, দেখতে এটিকে বাঁকানো কাঠের সাঁকো মনে হলেও এটি আসলে তৈরি করা হয় লম্বা সোজা কাঠের টুকরো দিয়ে, নিপূণ গানিতিক দক্ষতায়। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণে এটিকে মেথমেটিকাল ব্রিজ বলা হয়।
এগিয়ে যেতে লাগলাম ক্যাম্পাসের সরু রাস্তা দিয়ে, দূপাশে শত বর্ষের পুরনো ভবন। হঠাত একটি গলিপথের শুরুতে দেখলাম তির চিন্হ দিয়ে লেখা ট্রিনিটি কলেজ। পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। ছবি তোলার জন্য মোবাইল বের করতেই দেখলাম ফেসবুক থেকে নোটিফিকেশন এসেছে। বছর চারেক আগে আজকের এই দিনে প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম এসেছেন আমার কর্মস্থল সানশাইন গ্রামার স্কুলে এক অনুষ্ঠানে। কি অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা। এই ট্রিনিটি কলেজেই পড়েছেন এই বিজ্ঞানী। চার বছরের কোর্স দুই বছরে শেষ করে তাক লাগিয়েছেন বিশ্বকে। অধ্যাপনা করেছেন এখানে আঠারো বছর। হঠাত একদিন দেশের জন্য মন কাঁদায় ফিরে গেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।
আমাদের দেশ এখনো স্কলার তৈরি করছে। এই ক’দিন আগেও এখানে অধ্যাপনা করে গেছে আমাদের সানশাইনেরেই দুই ছাত্র ইয়াসির, ইয়ামিন। এখন তারা নাসায় গবেষনা করছে এরোস্পেস নিয়ে। দেশে এসে একমাস পর যখন আমি এই লেখা লিখছি তখন আমার আরেক ছাত্র আশফাক হামিদ, ক্যাম্ব্রিজে শুরু করেছে তার পি এইচ ডি গবেষনা। বাংলাদেশে বসে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ও লেভেল, এ লেভেলে World Highest পাওয়া আমার অসম্ভব প্রিয় আরেক ছাত্র ফারহান তানভীর ডাক পেয়েছে ক্যামব্রিজে তার কাজ নিযে কথা বলার জন্য। এ অসামান্য মেধাগুলি হয়ত কখনো আর দেশে ফিরে যাবে না। কিন্তু তাদের গবেষণায় উপকৃত হবে সমগ্র মানবজাতী। অদ্ভূত ভাল লাগায় মনটা ভরে গেল। মানুষ গড়ার কারিগরদের দলে থাকতে পারাটা সত্যি আনন্দের, হোক না ভূমিকাটা অতি ক্ষুদ্র।
কেম নদীতে হাঁসের সন্তরণ আর পেডেল বোটে টুরিস্টদের আনাগোনা দেখতে দেখতে কিংস কলেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। Corpus Clock এর সামনে এসে থামলাম কিছুক্ষণের জন্য, গ্রীক পুরাণের সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই অদ্ভূত কাঁটাবিহীণ ঘড়ি, আধুনিক কেমব্রীজের এক ব্যাতিক্রম আবিস্কার। এর নির্মাণ রহস্য আর কর্ম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নয়।
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুপরিচিত ভবন কিংস কলেজ চ্যাপেলের কাছে আসতেই এক বৃদ্ধা আমাদের এর ইতিহাস আর সম্মানার্থে জোরে শব্দ না করার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে দিলেন। ভেতরে ঢুকতেই অদ্ভূত শিহরণ লাগল। শতাব্দি প্রাচীন এই ভবনটি গোথিক ইংলিশ আর্কিটেকচারে তৈরি, ফেন ভল্ট ডিজাইনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। প্রতিবছর ক্রিসমাসে এখানে যে বিশেষ প্রার্থনা হয় তা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় সারা বিশ্বে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বসে পরলাম ফুটপাথে। ঠান্ডা ফলের রস হাতে বিশ্রাম নিয়ে চুমকু দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, আমরা বিখ্যাত গিল্ডহলের উঠোনে বসে আছি।
রেফায়েত কবির শাওন: প্রভাষক ইংরেজি। সানশাই গ্রামার স্কুল অ্যান্ড কলেজ। চট্টগ্রাম।